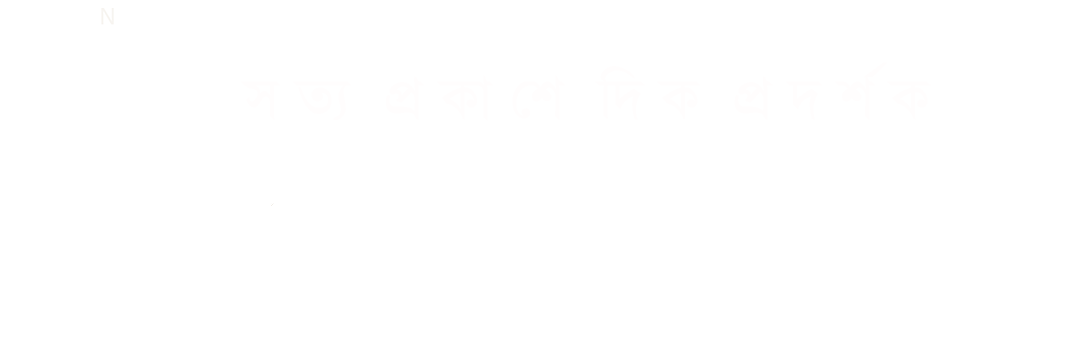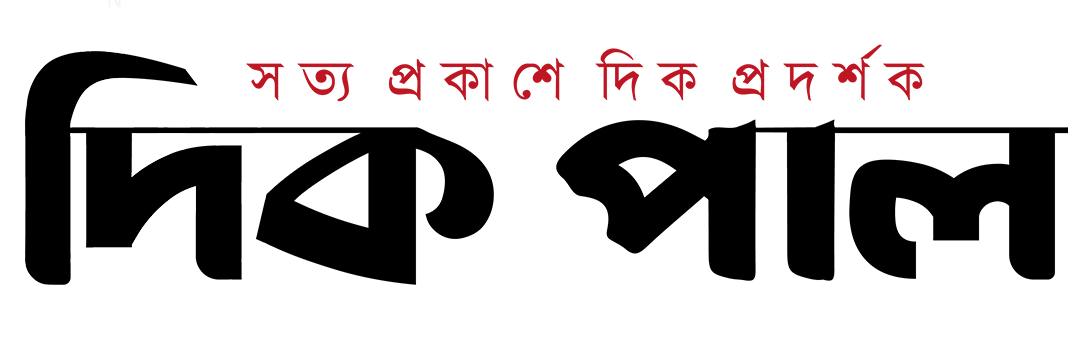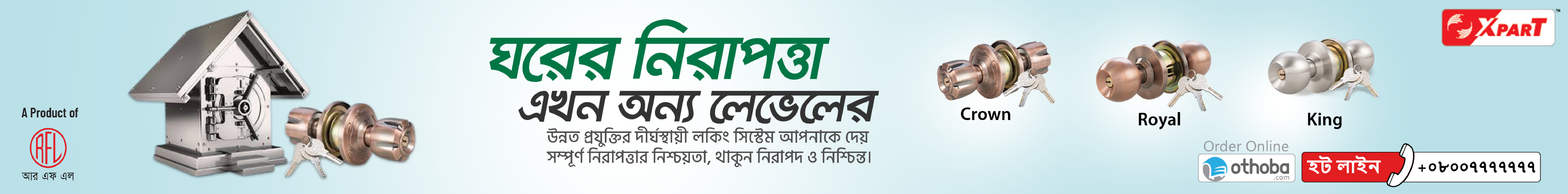যুদ্ধবিমান চালানো যেমন গর্বের, তেমনি চরম ঝুঁকিপূর্ণ। মুহূর্তের ব্যবধানে আকাশে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা, আর তখন পাইলটের বাঁচার একমাত্র উপায়— ইজেকশন সিট। তবে এই প্রযুক্তি প্রাণ বাঁচালেও, পাইলটের শরীর ও মন দুটোতেই ফেলে ভয়াবহ প্রভাব।
ইজেকশন মানে যুদ্ধের এক নতুন অধ্যায়, বলে জানান হার্ভার্ডে প্রশিক্ষিত মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ ডা. এ. কে. ঘোরি। তার মতে, ইজেক্ট করে বেঁচে গেলেও শুরু হয় দীর্ঘ পুনর্বাসনের লড়াই।
যখন কোনো যুদ্ধবিমান নিয়ন্ত্রণ হারায় বা দুর্ঘটনার মুখে পড়ে, তখন পাইলট ইজেকশন সিটের সাহায্যে নিজেকে অত্যন্ত উচ্চ গতিতে বিমানের বাইরে উৎক্ষেপণ করেন। এরপর প্যারাসুটের মাধ্যমে পাইলটকে মাটিতে নামিয়ে আনা হয়।
প্রাক্তন ফাইটার পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিট স্মিথ বলেন, ইজেকশন সিটের হ্যান্ডেল টানার পর বিমানের ককপিটের ক্যানপি খোলে, এবং আসনের নিচের রকেট পাইলটকে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ ফুট উপর দিকে ছুঁড়ে ফেলে। এই সময়ে শরীরকে ১৪ থেকে ১৬ জি-ফোর্স সহ্য করতে হয়— যা পাইলটের মেরুদণ্ডে তীব্র ধাক্কা সৃষ্টি করে।
এই রকেটচালিত উৎক্ষেপণের পর, সেন্সর অনুযায়ী উচ্চতা নির্ধারণ করে প্যারাসুট খোলে। বেশি উচ্চতায় একটু দেরিতে আর নিচু উচ্চতায় তাৎক্ষণিক প্যারাসুট খোলে। এরপর পাইলট আসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদে মাটিতে নামার চেষ্টা করেন।
তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে, আর সেখানেই লুকিয়ে থাকে চরম শারীরিক ঝুঁকি।
ইজেকশনের সময় সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে মেরুদণ্ডে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাইলটদের মেরুদণ্ডে ‘কমপ্রেশন ফ্র্যাকচার’ দেখা যায়, যেখানে মেরুদণ্ডের হাড় চ্যাপ্টা হয়ে যায়, কিন্তু তা স্থিতিশীল থাকে। এতে চলাফেরা সম্ভব হলেও তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়।
নিচু উচ্চতায় ইজেক্ট করলে পরিস্থিতি হয় আরও ভয়াবহ।
প্যারাসুট খোলার সময় না পেলে, মাটিতে আছড়ে পড়ার গতি কমানো যায় না। এতে ঘটে ভয়াবহ ‘বার্স্ট ফ্র্যাকচার’, যেখানে কশেরুকা ভেঙে যায় এবং মেরুদণ্ড অস্থির হয়ে পড়ে। এতে পাইলট চলাফেরা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেও পারেন না— এমনকি পা অবশ হয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ সময় এ ধরনের ইজেকশনে পাইলট মারা যান। আর যদি বেঁচে যান, তাহলে তাকে সার্জারি ও দীর্ঘ পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।
গবেষণা বলছে, ইজেকশনের শিকার পাইলটদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশের মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে। এদের অনেকে আর কখনও উড়তে পারেন না।
শরীরের পাশাপাশি, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন বেশিরভাগ পাইলট। ইজেকশনের অভিজ্ঞতা অনেকের মনে গভীর ট্রমা তৈরি করে।
ইজেকশনের পর পাইলটদের দাঁড়ানো ও হাঁটার সময় পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। এমআরআই ও সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে মেরুদণ্ডের ক্ষতি নির্ধারণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি শুরু করা হয়। মূলত প্যারাস্পাইনাল ও কোর মাসল শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়। পরে ফিটনেস টেস্টের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়— পাইলট আবার বিমানে ফিরতে পারবেন কিনা।
অনেক পাইলট গুরুতর চোটের পরেও চরম ধৈর্য, ফিজিক্যাল থেরাপি ও মানসিক শক্তির মাধ্যমে আবার ফিরতে সক্ষম হন। তবে এই পথ সহজ নয়— শুরু হয় ব্যথা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন আর দুর্ঘটনার ভয়াল স্মৃতির সঙ্গে বাঁচার নতুন জীবন।
ইজেকশনের মুহূর্তে পাইলটের হাতে থাকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। জীবনের তাগিদে নিতে হয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা পাইলটদের শুধুই আকাশে নয়, মাটিতেও করে তোলে এক একজন নায়ক।